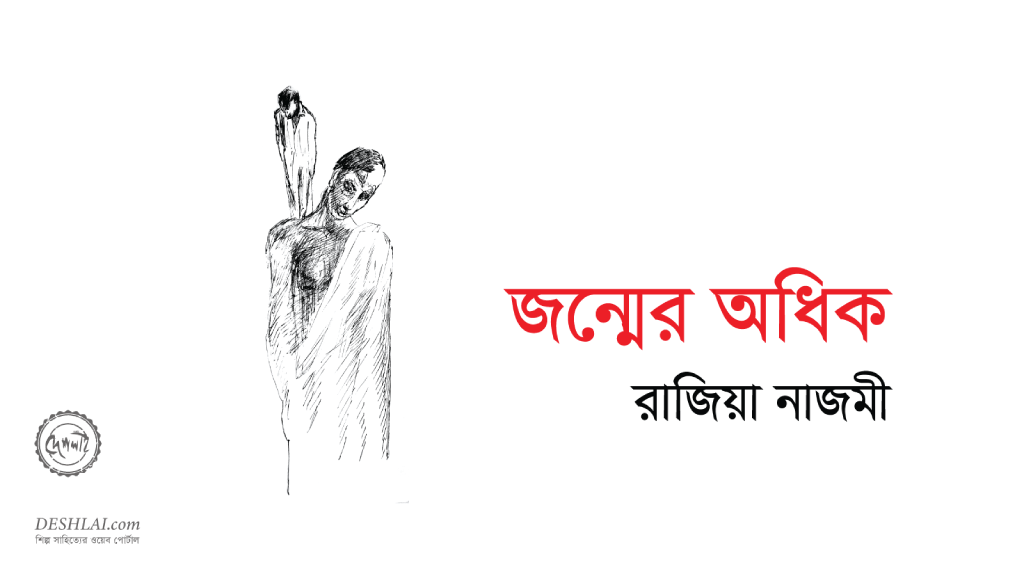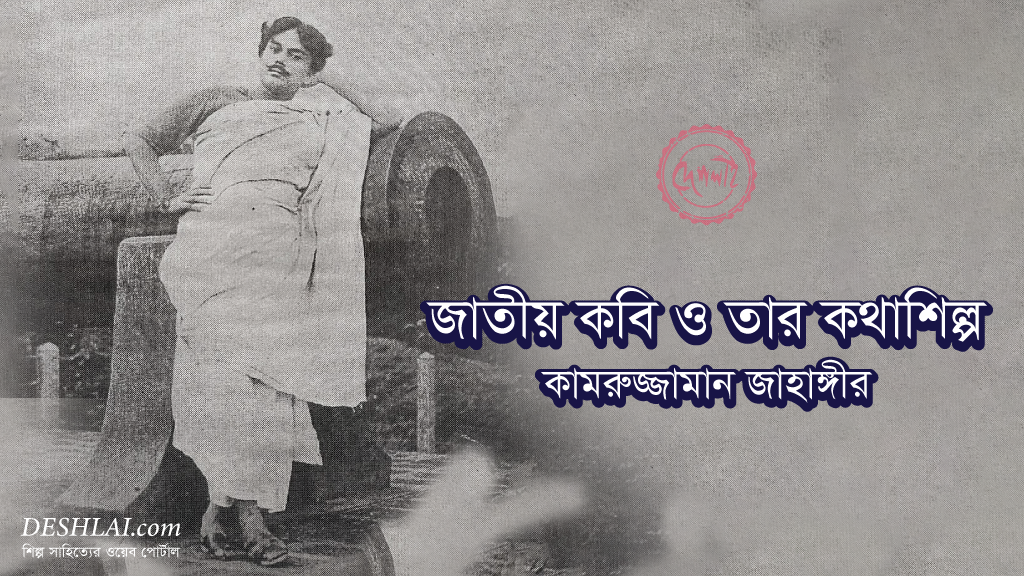
কাজী নজরুল ইসলামকে নিয়ে আমাদের আগ্রহের যেমন শেষ নেই, অনাগ্রহের একটা হিসাব-নিকাশ হতে পারে। আমাদের উপর আরোপিত প্রতিষ্ঠানের গুণে তিনি যেমন আমাদের আলোচনার মাঝাখানে থাকেন, তেমনি তার সারাজীবন আমাদের সারাজীবনকেও ভাবায়। সেই হিসাবে তিনি আমাদের আগ্রহ আর সংশয়ের ভিতর একটা দোলাচল জারি রাখেন। এমনতর রশি টানাটানি তার গুরু রবিঠাকুর নিয়েও হয়নি। আচ্ছা, নজরুল রবিঠাকুরকে গুরু কেন মানতেন বা গুরুকে হুলস্থূলের ভিতর কেন রাখতেন এও এক কৌতূহল বটে। তিনি কোনো হিসাব করে-টরে তা বলতেন বলে মনে হয় না। আসলে তিনি কোনোকিছুই একেবারে দাঁড়িপাল্লায় হিসাব করে করতেন না। তিনি হুজুগেরই কবি। তিনি পূর্বপাকিস্তান তো অনেক পরের ব্যাপার, পাকিস্তানিই কখনও কামনা করতেন বলে মনে করা মুশকিল। তবে তার প্রিয় পুত্র বুলবুলের অকালমৃত্যু, এর ফলে তার মনোজগতে তৈরি হওয়া ভাববাদী জীবন-আচার, দারিদ্রকে মেনে নেয়ার কালকে যদি সবাকে তিনি বাড়তে দিতেন, হয়ত তার ধর্মবাদী জীবন থাকে পাকিস্তান জিন্দাবাদের দিকেই নিয়ে যেত। তিনি আসলে যা চেয়েছিলেন তার নাম তাৎক্ষণিক মনস্কামনা। তিনি কখনও ধর্মের জন্য জেহাদ ঘোষণা করেননি। আবার কমরেড মোজাফফর আহমেদের সাথে লাঙল সম্পাদনা করলেও কমিউনিস্ট ভাবধারায়ও নিমগ্ন হননি। তিনি সবই হতে চেয়েও কিছুই হতে চাননি। এমনই এক কিছু না-চাওয়ার মানুষটাই এই জনপদের জাতীয় কবি। তাকে আমরা সাহিত্যমগ্নতায় কদ্দূর স্মরণ করি আর জাতীয় আচরণের অংশ হিসাবে কদ্দূর ভালোবাসি তা কিন্তু ভেবে দেখার বিষয়। আমরা যখন তাকে স্মরণ করি, কোন নজরুলকে স্মরণ করব, তা কিন্তু বের করা মুশকিলই। তিনিই বলছেন মসজিদেরই পাশে আমার কবর দিও ভাই, আবার বলছেন, শ্যামা মা তোর চরণতলে...। তিনি মুসলমানদের কথা লিখছেন মোসলেম ভারত-এ; আবার সনাতন হিন্দুধর্মের ঐতিহ্য লিখছেন উপাসনা নামের পত্রিকায়। আবার হিন্দু-মুসলমানের ঐক্যের কথা জানিয়েও প্রবন্ধ লিখেছেন। দর্শনের দিক থেকে তার কোনো স্থিরতা ছিল না। ভাবের দিক থেকেও একটা নির্দিষ্ট আচরণে তাকে বাঁধা যায় না। তবে তিনি ভালোবাসাকে ভালোবেসেছেন। এ যদি কোনো ব্রত হয়, জীবনসাধনা হয়, নিজের ঈশ্বরত্ব নির্মাণের পথচলা হয়, তা তিনি তার আচরণে রাখতে পেরেছেন। তিনি লিখছেন, ‘আমার কর্ণধার আমি। আমায় পথ দেখাবে আমার সত্য। আমার যাত্রা শুরু করার আগে আমি সালাম জানাচ্ছি। নমস্কার করছি আমার সত্যকে। ... নিজেকে চিনলে, নিজের সত্যকে নিজের কর্ণধার মনে জানলে, নিজের শক্তির উপর অটুট বিশ্বাস আসে।’ আমি নজরুলের সত্যের কাছে, বিশ্বাসের কাছে গভীর আগ্রহ নিয়ে থাকিয়ে আছি। দেখি, নজরুলের কথাশিল্প আর তার প্রকাশিত সৃজনশীলতা সত্যের আদল নির্ণয় করতে পারে কিনা। তবে এটা আবারও বলতে হয়, তিনি প্রেমব্যাকুল এক সত্তা। সেই সত্তার বিশেষত্ব নির্ণয়ের বাসনা আমার মন-মাজারে জারি থাকল।
যারা কথাশিল্প চর্চা করছেন, নজরুলের প্রভাব কি তাদের উপর আছে? তার কথাশিল্প পাঠ কেমন হচ্ছে। এও প্রশ্ন হতে পারে একজন সৃজনশীলমানুষের অন্তর্জগৎ দেখতে চাইলে এটা কি খুব জরুরি একটা বিষয়। আমার মনে হয়, এটাও একটা বিষয় বটে। আমি সাহিত্যমগ্ন বুকস্টলের সারি সারি বইয়ের ভিতর নজরুলের কথাশিল্প খুঁজি- নাহ্, তেমন গ্রন্থ তো পাই না। দুই-একটা গ্রন্থ থাকলেও তা নিয়ে তেমন নাড়াচাড়া দেখি না। যারা কথাশিল্প চর্চা করছেন তারা তার লেখালেখি নিয়ে কেমন কথাবার্তা বলছেন, এবার তা স্মরণ করি। তাও খুব বেশি কিছু নয়। বরং বলা যায়, একাডেমিক পড়াশুনা আর নজরুলের জন্ম-মৃত্যুবার্ষিকীতে গল্পের নাট্যরূপ আমরা দেখছি- ‘পদ্মগোখরো’, ‘রাক্ষুসী’, ‘স্বামীহারা’, ‘রিক্তের বেদন’, ‘ব্যথার দান’, ‘মেহের-নিগার, ‘হেনা’, ‘রাজবন্দির চিঠি’ ইত্যাদি। আমি তার গল্পসমূহ খেয়াল করে দেখেনি এর সবগুলোর পাঠস্বাদুতা, বাক্যবিন্যাস, বানান, এমনকি চিহ্নপ্রয়োগ প্রায় একই আছে। নজরুলের সাহিত্যিক-বয়স বাড়ছে, কিন্তু সাহিত্যের চেহারা কিন্তু একই আছে। এ খুবই আশ্চর্যের বিষয় যে একই তালের গল্পভুবন আমরা প্রত্যক্ষ করতে থাকি।
বাঁধন-হারা, কুহেলিকা, মৃত্যুক্ষুধা- এই তিনটিই নজরুল সৃজিত উপন্যাস। প্রত্যেকটিই হয়ত ৫-৬ ফর্মার সৃজনকর্ম। তবে তিনটির অবয়বে আলাদা আলাদা ধরন আছে। এসবের বিষয়বস্তুও একেবারে আলাদা। আমি যদ্দূর জানি বাঁধন-হারা বাংলাসাহিত্যের প্রথম পত্র-উপন্যাস। তিনি যে হাবিলদার হিসাবে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন এটি মুখ্যত তারই বয়ান। নুরুল হুদা, রাবেয়া, সোফিয়া, সুহাসিকা, রবিয়্ল, মাহবুবা ইত্যাদি চরিত্রের ভিতর চিঠি চালাচালি হলেও, যুদ্ধ-ময়দানের নিঃসঙ্গতা প্রকাশ পেলেও তাতে যুদ্ধের কোনো বর্ণনা নেই, যুদ্ধের হিংস্রতা বা ভয়-ব্যাকুলতা তো নেইই। যা আছে তার নাম ব্যাকুলতা। বরং বলা যায় ব্যাকুলতাই এ উপন্যাসের প্রধান অনুসঙ্গ। আমরা এর ভিতর জার্নির মাধ্যমে আলাদা এক শিল্পরূপকে সরেজমিনে চিহ্নিত করতে পারি- সে হায়, সেই যে আমাদের চিঠির যুগ! সেলফোন, এসএমএস, ইন্টারনেট, চ্যাট ইত্যাদির যুগে আমরা চিঠির সেই মাদকতা আর মনে করতে পারি না। এ উপন্যাসে সেই যুগকেই শুধু পাওয়া যায় না; নজরুলের অন্তর্দাহ যেন তাতে জলজ্যান্ত হয়ে আছে। সারা পৃথিবীর প্রতিই যেন নূওট্টল হুদা বা নজরুলের ক্ষোভ একেবারে জমাট বেঁধে আছে। চিঠির প্রতি স্তরে স্তরে তাই উন্মুক্ত হতে থাকে। তিনি যে আগুন নিয়ে ঘুরছেন - আরবের মরুঅঞ্চল থেকে মেসোপটেমিয়া, তপ্ত-হাওয়ার যেখানেই গেছেন সবকিছু তছনছ করে দিতে চায় সে। কী যে ভয়ঙ্কর সব মনোযাতনা। তার বর্ণনার নিপুণতা অনেকটাই একেবারে প্রাণজাগানিয়া অবস্থায় আছে। নজরুলকে জানার জন্য, তার সর্বময় জীবনের প্রাথমিক পর্যায়ের স্পর্শ নেয়ার জন্য এ উপন্যাসের গুরুত্ব অনেকটাই বলা যায়।
নূরুল হুদা যেন নজরুলের জীবনরূপ। তার পিতৃহারা বেদনা, মায়ের কাছে আসতে না-পারার বিপুল-আকুলতা এখানে বার বার প্রকাশ পেয়েছে। আর যা থাকার, মানে নজরুলের সৃষ্টিসুধার অনন্য সম্পদ, সেই প্রেম তো আছেই। মাহবুবা, সোফিয়া আর সুহাসিকার প্রতি কী যে আকুল-ব্যাকুল টান আমরা দেখি। তবে যুদ্ধসময়ের মানুষের মানবিক, জৈবিক সম্পর্কের নানান টানাপড়েন কখনও কখনও তাতে আলোকিত হয়েছে। একপর্যায়ে আমরা জানতে থাকি যে সোফিয়ার ভীষণ অসুখ। হয়ত সে বাঁচবে না। মাহবুবার সংসার গুঁড়া-গুঁড়া হয়ে গেছে- এখন তার বৈধব্য দশা। তবে এখন সে নিজেই বিশাল জমিদার। তারও সুখ নেই। সংসারে তার মন নেই। তাই সে দেশ থেকে দেশান্তরে যেতে চায়। অথচ নূরুল হুদার সৈনিক-জীবনকে যথার্থ করার জন্য সেই তাকে যুদ্ধে পাঠায়। হায়রে জীবন, কষ্ট কিছুতেই যায় না। এমন নানান গৃহপালিত কষ্টের ভিতর দিয়ে যুদ্ধের ভিতর বিচরণ একটা জীবনআলেখ্য শেষ হয়। নূরুল হুদা ফেরে না। আমরা তবু স্মরণ করি তার যাপিত সময়ের কথা। তার কষ্টের কথা, একটা বছর তার কেটেছে ইরাকের মরুপ্রান্তরে, ফোরাতের কুলে কুলে, শুকনা পর্বতের অস্থিশ্মশানে। একসময় তার ক্লান্তি আসে, চিঠিও লিখতে মন চায় না তার। বেশি বেশি চিঠি পাওয়ারও ভয় তার, দুঃসংবাদ পাওয়ার ভয়। তার এমনই মানসিক বৈকল্য ছিল যে সে ভ্রাম্যমাণ আমিক্যাম্প অনেক চিঠি পড়েইনি! তবে এরই ভিতর আমরা জানতে পারি, আবারও যুদ্ধে থাকার কাগজপত্র রিনিউ করে সে। তিনবছর সে তথায় থাকবে। সাহসিকাকে শেষ কথাগুলি এভাবেই নজরুল ওরফে নূরুল হুদা বলেন, ‘আশীর্বাদ ক’রো তোমরা সকলে, আবার যখন আসব রঙ্গমঞ্চে- তখন যেন আমার চোখের জলে আমার সকল গ্লানি, সকল দ্বিধা-দ্বন্দ্ব কেটে যায়- আমি যেন পরিপূর্ণ শান্তি নিয়ে তোমাদের চোখে চোখে থাকাতে পারি।’
এটা খুবই ব্যাকুল-আশ্চর্যের বিষয় যে যেই নজরুল সারাটা জীবন পার করল বৃটিশদের বিরুদ্ধে লড়াই-সংগ্রাম করে তাকে আবার যুদ্ধে অংশ নিতে হ’ল। তিনিই তো কবিতার জন্য জেল খেটেছেন। প্রতিনিয়ত স্বোপার্জিত পথে তার দ্রোহ বজায় রাখতে চেয়েছেন। তার যে সৃজনশীলতার ধরন তাতে তার যুদ্ধে যাওয়াটা আবার বিস্ময়-ক্ষোভ, এমনকি হতাশারও জন্ম দিতে পারে। তিনিই আবার একেবারে সুবাস বসুর স্টাইলে ইংরেজ-হটাওয়ে নিয়োজিত ছিলেন।
কুহেলিকা নজরুলের আরেক কুহেলিকাময় সৃষ্টি। আমরা এর সৃজনবৈশিষ্ঠ্য নিয়ে বেশি কথা বলতেই চাই না। কারণ এর শরীর, বর্ণনাভঙ্গি এতই শৈথিল্যমুখর যে এ নিয়ে কথা চালিয়ে যাওয়াই মুশকিল। এখানেও প্রেম আছে। জাহাঙ্গীর আর তাহমিনা নামের দুই চরিত্রের প্রেম। তাদের জৈবিকতায় উনবিংশ শতাব্দীর ভীরু থরথর কম্পনের জলজ প্রেমকে তারা অস্বীকারা করতে পেরেছেন। তারা পরস্পরকে শারীরিকতায় ভর করে, জৈবিকতায়, সাহসে বেলাজে ভালোবাসতে পেরেছেন। তাদের ভালোবাসার সৃষ্টিশীলতা উপন্যাসটির অসহায়তার ভিতর খানিক দাপট সৃজন করতে পেরেছে। এবার উপন্যাসটির উপজীব্যতা নিয়ে কথা বলি। এটি সন্ত্রাসবাদকে নিয়ে গড়া একটি উপন্যাস। এও নজরুলের স্বকীয় সৃষ্টিই। এখানে তিনি মুসলমান সমাজের স্বাভাবিক প্রবণতার ধার ধারেননি। আমরা উনবিংশ শতাব্দীর যে যুববিদ্রোহ বা ইংরেজদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র আন্দোলন দেখি তা মূলত গড়ে উঠেছিল যুবকংগ্রেসের একটা অস্ত্রপাগল অংশ সহযোগে। তারা ইংরেজ কর্তাব্যক্তিদের উপর প্রত্যক্ষভাবে, এমনকি তাদের স্থাপনার উপর সরাসরি আক্রমণ করে। এদের মূল অংশ হিন্দু জাতীয়তাবাদঘেঁষা কংগ্রেসের মাধ্যমে হওয়াতে তাতে স্বভাবতই মুসলমান সমাজ তাতে অংশ নেয়নি। তারা ততদিনে মুসলিমলীগ আর কৃষকপ্রজা পার্টির ছায়াতলে একত্রিত হয়ে ইংরেজ কলোনিয়াল শাসন আর শাসনব্যাকুল, পেষণমুখর হিন্দু-জমিদারদের কবল থেকে মুক্ত হতে চাইছে। তারা পাকিস্তান চাইছে মুসলমান হওয়ার জন্য নয়, বরং উল্লিখিত দুই ধরনের পেষণ থেকে মুক্ত হওয়ার মানসে। এমনকি এই আন্দোলন নিয়ে এমন প্রচারণাও জোরদার ছিল যে সন্ত্রাসবাদীরা মা কালীকে সাক্ষী রেখে, নিজেদের রক্তের শপথ নিয়ে এ আন্দোলনে শরিক হয়। ফলে মুসলমান সমাজের অগ্রসর মধ্যবিত্তও এ থেকে দূরে থাকেন। তবে নজরুলের বিষয়টি বরাবরই আলাদা- তিনি ছিলেন তাৎক্ষণিক আবেগের লোক। তাই তো তিনি যুগান্তর আর অনুশীলন দলের সাথে নিজের বিবেচনাক্রমে সন্ত্রাসবাদের প্রতি আস্থা রাখেন। মুসলমান সম্প্রদায়ের কেউ তো এমনকি করবেই না। তাহলে এ নিয়ে এমন একটা সমাধানে আসাই যায় তিনি ছিলেন স্বোপার্জিত স্বাধীনতার প্রতীক। তিনি নিজের মতো করে সত্য খুঁজতেন। তবে সবচেয়ে মুশকিলের কথা হচ্ছে, নজরুল নিজেও যেন নির্ণয় করতে পারেনি যে সত্য কারে কয়। তার চেহারা-সুরত কেমন হবে!
আমরা এ ক্ষেত্রে আরও কিছু উপন্যাসের কথা স্মরণ করতে পারি যেখানে সন্ত্রাসবাদ মূল উপজীব্য করা হয়েছে। আমরা অতি সহজেই শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের পথের দাবির কথা বলতে পারি। এ গ্রন্থে পথের দাবির আর শেষ নেই। এর মূল নায়ককে মনে হবে এ কালের নায়ক, যেন আধুনিকতার শরীর বেয়ে বিপ্লবের এক নিরাকার সাধক নাজেল হয়েছেন। তিনি সবই পারেন। পৃথিবীর সব ভাষাই তিনি জানেন! বাস্তবে তা সম্ভব কিনা, আমরা এ নিয়ে চ্যালেঞ্জ করতে চাই না। কারণ সাহিত্যের সত্য এক বিকল্প সত্য। তা সত্য হতেই হবে, সত্যের কোলঘেঁষে এতিমের মতো দাঁড়িয়ে থাকতে হবে, তারও কোনো মানে নেই। তবে মজার ব্যাপার হচ্ছে, শেষ পর্যন্ত সব্যসাচী নামের চরিত্রটির পথের দাবির পূর্ণ অবয়ব আমরা নির্ণয় করতে পারি না। অন্যদিকে গান্ধির প্রতি দারুণ ব্যাকুল রবিঠাকর তো সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে দশ হাত নিয়েছেন। এমনকি তাদেরকে চোর-বাটপার বানাতেও তার কোনো অসুবিধা হয়নি। সতীনাথ ভাদুড়ির জাগরি আর ঢোড়াইচরিত মানসের দ্বিতীয়ভাগেও সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপে নিমগ্ন হতে দেখি। সন্ত্রাসবাদ বিপ্লবের একটা কঠিনতম পর্যায়। প্রশাসন বা প্রতিষ্ঠানের ছি বা আরও বেশি করে বললে, সৃজনশীলতার সাথে রাষ্ট্রের একটা সংঘাত কিন্তু অপরহিার্য। রাষ্ট্র তার অন্তর্প্রবাহের দায়ে, আচরণে, কাঠামোয় বা ভদ্রতায় নমীয়তার পূজা করবেই। কিন্তু সত্য নির্মাণে ব্রতী যে জন তার মনে, সামাজিকতায়, রাষ্ট্রীয় আচরণে, এমনকি ব্যক্তিজড়তায় নতুন কিছু গড়ার সেই প্রত্যয়ে। এর সাথে সৃষ্টির একটা দ্বন্দ্ব অপরিহার্য। নজরুলের প্রেমব্যাকুল সন্ত্রাসবাদী চরিত্র জাহাঙ্গীরের মন-মাজারে আমরা তা কিন্তু পাই। নিজেকে নির্মাণের, ভালোবাসায় বিকল্প সত্য সৃজনের তাগিদ তার আছে। এইভাবে দেখলে নজরুলের কুহেলিকা একটা দরকারি উপন্যাস। হয়ত নতুন কিছু গড়ার দাপুটে আচরণে কথাশিল্পের সেই মনোহর শিল্পতা নাই। কিন্তু নতুন করে নিজেকে দেখার জীবন তো আছে। তাই বা কম কি! আমরা শিল্পমানের বিষয়টা বাদ দিয়ে জীবনের নবতর স্পন্দনের বিষয়টা ভাবনায় নিয়ে এলে পর, কুহেলিকার প্রতি একধরনের দায়বদ্ধতা আমরা অনুভব করতেও পারি। জীবনকে নানাভাবেই দেখা যেতে পারে। আমরা এটা ধরতে পারি যে এও জীবনকে দেখার, বা চেখে চেখে অনুভব করার অতি কার্যকর একটা বিষয় বটে। বিপ্লবকে অনুসন্ধান বা প্রয়োগের চেয়ে নেয়ার মহোত্তম কিছু কি থাকতে পারে!
জাহাঙ্গীর নামের চরিত্রটি কিন্তু এক ঝাপসা-ধুয়াশাময় চরিত্র। তার জন্মের হদিস পাওয়া মুশকিলই। আমরা শেষ পর্যন্তু এটুকু জানতে পারি যে তার জন্মইতিহাস কোনো সুস্থ পথে বা আমাদের প্রচলিত বিধিবিধানের আওতায় তা পড়েনি। তবে গোরার জন্মইতিহাসকে নিয়ে রবিঠাকুর যেমন নানান কৌশলের অবলম্বন করেছেন, মাহাত্ম্য আরোপ করতে চেয়েছেন, কলোনিয়াল ধ্যান-ধারণা থেকে তিনি একেবারে মুক্ত হতে পারেননি, নজরুল তা করেননি, কোনো মহত্ত এখানে নেই, বরং পরিচয়হীন জন্মের এক দগদগে ঘা তিনি প্রকাশ করতে পেরেছেন। এখানে নজরুলের একধরনের আলোকময়তা প্রকাশ পেয়েছে। আবারও বলতে হয়, শিল্পের ঘোর না থাকলেও, বর্ণনার সরলচঞ্চলতা থেকেও জীবনকে দেখার কুহেলিকা অনেক গৌরবমুখর।
নজরুলের মৃত্যুক্ষুধা অনেকটাই পরিপক্ব রচনা। এখানে জীবনের কথা, তার নানা বাঁক, বাঁকদদলের নানান ইশারা শিল্পময়তায় প্রকাশ পেয়েছে। এটিই বোধ করি নজরুলের জনপ্রিয় উপন্যাস। মানববিকাশের স্বার্থে, জীবনকে একেবারে গভীরভাবে দেখার বিষয়টা এখানে ভালোভাবেই প্রকাশ পেয়েছে। এখানকার বর্ণনা নজরুল নিজেকে একেবারে ছাড়িয়ে গেছেন, অসাধারণ কিছু সৃজন করে ফেলেছেন তা কিন্তু নয়। তবে যে জীবন তিনি এখানে এঁকেছেন, ক্ষুধার কথা বলেছেন, মৃত্যুর ভয়াবহতা দেখিয়েছেন, ধর্মান্তরের মতো কঠিন-জটিল বিষয় একে একে অঙ্কন করেছেন, খ্রিষ্টধর্ম বিস্তারের কথা বলেছেন তা বেশ দরকারি অনুসঙ্গ হয়ে গেছে। নজরুল এখানে উনবিংশ শতকের প্রথম দিকের কৃষ্ণনগর, জীবনপ্রবাহের জটিলতা, খুঁটিনাটি অনেক বিষয়, মধ্যবিত্তের টানাপড়েন, তখনকার ঠাকুরবাড়ির বাবু-কালচারের দিকে ঝুঁকতে থাকা মধ্যবিত্ত তিনি আমাদের সামনে জলজ্যান্ত করেছেন। মধ্যবিত্তের একটা অতি প্রয়োজনীয় বিষয় হচ্ছে, বাইরে ডাট বজায় রাখা আর ঘরে দুরন্ত কাইজা-ফ্যাসাদ করে যাওয়া। তা এ উপন্যাসটিতে আছে। এর ভাষায় তেমন কিছু নেই। তিনি কোনো উপন্যাসেই ভাষার দিকটা বিশেষ বিবেচনায় আনতে পারেননি। অথচ ততদিনে আলালের ঘরের দুলাল আর হুতুমপ্যাঁচার নকশার মতো বৈঠকি মেজাজ ভাষায় ছিল। উপন্যাসটি যেন এমনতর ভাষার জন্য ব্যাকুলতাও প্রকাশ করছিল। কিন্তু নজরুল কোনো রিস্ক নেননি। তবে কথাক্রমে এও বলতে হয়, এখানে যে ভাষাটা তিনি ব্যবহার করছেন, তা ওই সময়কার সাহিত্যিক এ্যাস্পেক্টে তেমন গুরুত্ব নেই; কিন্তু তা মুসলিম-জাতিগোষ্ঠীর ব্যাকডেটেড রূপকে সামনে আনার দিক থেকে মর্যাদা নিশ্চয়ই আছে। কারণ তখন মুসলমানরা আরবি-ফার্সির হুজুরত্ব ছেড়ে মায়াময় বাংলার দিকে হৃদয়-মন-শরীর ফেরাচ্ছেন। আর নজরুলের ভাষারূপ সেখানে টনিকের মতোই কাজ করছে। আসলে নজরুল কলকাতা-কৃষ্ণনগর-ঢাকার তখনকার ভিতরকার নিজস্ব ক্রোধকে চিহ্নিত করতে চাননি। যে সমাজ ক্রমশ ভাগ হয়ে যাচ্ছে, হিন্দু-মুসলমানের দূরত্ব ব্যাপকহারে বাড়ছে, তা দেখেও দেখেননি তিনি। কী যে দারুণ ক্ষুধা, সেই ক্ষুধায় মানুষ খ্রিস্টান হচ্ছে, নিজেদের ভিতর আরেক দুুনিয়া গড়ে উঠছে, একদিকে রামমোহন-রবিঠাকুর-কেশববাবুদের ব্রাহ্মসমাজ সনাতন ধর্মের ভিতর ঈশ্বর ঢোকাচ্ছেন; অপরদিকে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দরা ভারতমাতার বন্দনারূপে মা জগৎকালীকে পূজা করছেন, সকল-ধর্মমতকে মায়ের ছায়াতলে আশ্রয় দিচ্ছেন। সেইসব জটিল-রাজনৈতিক অবস্থাকে নজরুল যেন ইচ্ছা করেই সামনে আনেননি। বরং তিনি হিন্দু-মুসলমানের ভিতর একটা বন্দনা জারি রাখতে চেয়েছেন। তাও যেন নানান জারিজুরিতে নড়বড়ে হয়ে যাচ্ছে!
যাই হোক, এখানে শুধুু ক্ষুধাই নেই, সংসারদারি, আশমানদারি, প্রেম ভালোবাসা আছে। তিন সতীনের নিরামিষ মার্কা নীরব-জীবন আছে, তাদের বৈধব্যকে পরম মমতায় লালন করার মতোই অবিশ্বাস্য এক শাশুড়ি আছেন। তবে মানুষের হাহাকার, জীবনকে লালনের বিষয়টা আছে, আছে আনসার নামের এক সময়োপোযোগী চরিত্র। তার পোশাক-আশাক আর বিধবার প্রতি অহেতুক খোঁজ-খবর নেয়া বাড়তি কিছু মনে হলেও তার ভিতর চলনে-ফিরনে প্রাণ আছে- সময়ের দাবি মেটানোর তাগাদা আছে।
উপন্যাসে নজরুল নিজেকে প্রকাশের ব্রত নিয়েছেন যেন; মৃত্যুক্ষুধার আনসার, কুহেলিকার জাহাঙ্গীর এবং বাঁধন-হারার নূরুল হুদার ভিতর কোথাও নো কোথায় লেখকের ব্যক্তিজীবন আছে। ব্যক্তিজীবন থাকাটা কোনো অদরকারি বা বাড়তি কিছু নয়; তবে একেবারে বাবে বারে প্রকাশ্যে নিজেকে নাজেল করার ভিতর একধরনের অসহিষ্ণুতা আছে বলা যায়। তবে নূরুল হুদা যেভাবে কা-জ্ঞানহীনভাবে প্রেমের পূজা করে, জাহাঙ্গীর বা আনসারে তা নেই। আনসার তো আবার বিপ্লবীও বটেÑ শ্রমিক সংঘ করে, মার্কস-এঙ্গেলস-লেনিন এমনকি ট্রটস্কিও তার সাধনার ভিতর আছে। স্ট্যালিন না থেকে ট্রটস্কি কেন আছেন তা অবশ্য নজরুল ক্লিয়ার করেননি। এ চরিত্রসমূহের ভিতর একটা জায়গায় মিল আছে, আর তা হচ্ছে, তাদের ভিতর নারীর প্রতি ব্যাকুল হাহাকার আছে। উপন্যাস তিনটির শেষও হয়েছে অতি-তৎপর ভালোবাসার প্রতি টান রেখে। যেন সবই প্রেমেই তার কার্যকারিতা বজায় রাখতে পারে! এ থেকে আমরা এ প্রশ্ন করতে পারি, তিনি কি অন্তর্জগতে মৈথুনতা বিষয়ে আলাদা কোনো ধারণা লালনা করতেন? তিনি যে তবে ফ্রয়েডিয় তৎপরতা লালন করতে তা বলাও মুশকিল। তিনি অরূপে রূপের মহিমা খোঁজেননি। তিনি তো জলজ্যান্ত রূপময়তায় তার ব্যাকুলতা প্রকাশ করেছন। তবে তার ছিল পক্ষপাতা ছিল কামময়তায়, প্রকাশ্য প্রেমে; প্রেমই আত্মার মুক্তি খুঁজতেন তিনি। তিনি যেন জীবনপ্রেমের পূর্ণ প্রাপ্তির ভিতর কোথায় যেন অপ্রাপ্তির সন্ধান করছেন! এই যে হাহাকার, এই যে জীবনের অপ্রাপ্তিকেই খোঁজার একটা প্রয়াস তা হয়ত তার ব্যক্তিজীবন থেকেই নাজেলকৃত। তাই তো তার উপন্যাস বা গল্প যাই হোক, হাহাকারমুখর জীবনের একটা মীমাংসা আনতে চেয়েছেন। এ দিকটাই তার কথাশিল্পের অন্যতম প্রয়োজনীয় অনুসঙ্গই বলা যায়।
১৪.৮.১২